ভিডিও হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যেখানে ছবিগুলোকে চলমান দেখা যায়। যাঁরা এই বিষয়ে একেবারে নতুন, তাঁরা জেনে অবাক হবেন যে ছবি কিন্তু চলমান হয় না। প্রকৃত পক্ষে ছবি চলমান নয়, চলমান হওয়া মনে হয় মাত্র, এটা এক ধরনের ইলিউশন।

ফটোশপে একটা ছবি আঁকানো হল। ছবিটির মাঝখানে একটি খাঁড়া রেখা আঁকানো আছে। রেখাটিকে প্রতিবার ৫ ডিগ্রি করে ঘুরিয়ে আরো ২৪টি ছবি বানানো হল। মোট ছবি দাঁড়ালো পঁচিশটি। কম্পিউটার মনিটরে যদি এই পঁচিশটি ছবিকে বেশ দ্রুত একটির পর আরেকটি দেখা যায়, তবে মনে হবে, রেখাটি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে। একটি ছবির পর আরেকটি ছবি দেখা হচ্ছে, সেটা উপলব্ধি হবে না। বলা চলে আঁকানো ছবি দিয়ে এটা একটা ভিডিও বানানো হল ।
যখন এক সেকেন্ডে ২৫টি ছবি পরপর দেখানো হয়, তখন এটাকে চলমান ছবি মনে হয়। যদি প্রতি সেকেন্ডে ২৫টি ছবি না দেখিয়ে এর চেয়ে অনেক কম, মাত্র ৫টি ছবি দেখানো হয়, তখন রেখাটিকে ঘুর্ণায়মান মনে হবে না, মনে হবে একটি ছবির পর আরেকটি ছবি দেখছি।
কোনো ক্যামেরায় যখন ভিডিও ধারণ করা হয়, তখন ক্যামেরাটি প্রতি সেকেন্ডে ২৫টি (পাল কালার এনকোডিং সিস্টেমে) করে ছবি ধারণ করে। যদি ১০ সেকেন্ড ধরে ভিডিও ধারণ করা হয়, তবে এই ১০ সেকেন্ডে ক্যামেরাটি মোট ২৫০ ছবি তোলে। যদি ১০ সেকেন্ড ধরে আমরা ঐ ভিডিওটি দেখি, প্রকৃত পক্ষে ২৫০টি ছবি পরপর দেখি, আমাদের মনে একটি চলমান চিত্রের ইলিউশন তৈরি হয়।
ভিডিও’র ইতিহাসে আমি যেতে চাই না। ফটোগ্রাফি আবিষ্কার এবং চালু হওয়ার পরই যে ভিডিওগ্রাফি এসেছে, এটা নিশ্চিত। একসময় শব্দবিহীন ভিডিওচিত্র ধারণ করা যেত। এই ভিডিও তৈরি করার সময় একটি ক্যামেরায় ভিডিও রেকর্ড করা হত ভিন্ন একটি যন্ত্রে শব্দ রেকর্ড করা হত; পরে ভিডিও’র সাথে মিলিয়ে শব্দ স্থাপন করা হত। পরে ক্যামেরাগুলোতে অডিও (মানে শব্দ) রেকর্ড করার সুবিধা যোগ করা হয়েছে। এখন ক্যামেরায় ভিডিও করলেই অডিও রেকর্ড হয়।
খুব বেশি দূরের কথা নয়, ডিজিটাল ক্যামেরা চালু হওয়ার পরও ছবি তোলার ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও ধারণ সম্ভব হত না। আমরা দেখেছি দশ-পনের বছর আগেও ডিজিটাল ক্যামেরাগুলো দিয়ে শুধু স্থির চিত্রই তোলা সম্ভব হত, ভিডিও নয়। এখন (২০২২ সালে) সকল ব্র্যান্ডের সকল মডেলের ক্যামেরায় ভিডিও ধারণের ব্যবস্থা রাখা হয়। রেকর্ডিং শুরু করার জন্য আলাদা বাটনও থাকে। তার মানে যাঁদের স্থিরচিত্র তোলার কোনো ডিজিটাল ক্যামেরা আছে, এমনকি মোবাইল ফোন আছে, তাঁরা সবাই এখন ভিডিওগ্রাফি চর্চা করতে পারেন, প্রফেশনাল মানের ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ক্যমেরাগুলোতে যে অডিও রেকডিং সুবিধা আছে, তাতে ভালো মানের অডিও রেকর্ডও করা যায়। প্রত্যেক ক্যামেরায় বিল্ট ইন মাইক্রোফোনতো আছেই, এক্সটারনাল মাইক্রোফোন সংযুক্ত করার ব্যবস্থাও আছে।
ভিডিওগ্রাফিতে কিছু ব্যবস্থা এবং কিছু শব্দ
(১) এফপিএস: ফ্রেমস পার সেকেন্ড। ক্যামেরা প্রতি সেকেন্ডে কতটি ছবি তুলে ভিডিও রেকর্ড করবে। ভিডিও ধারণের আগে ক্যামেরায় এই এফপিএস সেট করতে হয়। এফপিএস বিভিন্নরকম আছে; যেমন:
২৫ এফপিএস, যা প্যাল PAL কালার এনকোডিং সিস্টেমে টেলিভিশন ব্রডকাস্টের উপযোগী। আমাদের দেশসহ এশিয়ার কিছু দেশে PAL কালার এনকোডিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।
৩০ এফপিএস, যা NTSC কালার এনকোডিং সিস্টেমে টেলিভিশন ব্রডকাস্টের উপযোগী। ইউরোপ এবং অ্যামেরিকা মহাদেশের কিছু দেশে NTSC কালার এনকোডিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।
আমাদের দেশে ২৫ এফপিএস সেট করে (প্যাল PAL সিস্টেমে) তৈরি করা কোনো ভিডিও ইউরোপের ঐ সব দেশের কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করতে হলে সেটাকে NTSC কালার এনকোডিং সিস্টেমে কনভার্ট করে নিতে হবে।
৫০ এফপিএস এবং ৬০ এফপিএস সাধারণত বিশেষ বিশেষ ভিডিও ইফেক্ট দিতে এবং গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় ।
(২) ভিডিও’র রেজ্যুলেশন: এটা প্রকাশ করে ভিডিও’র প্রতিটি ইমেজের পিক্সেল ডাইমেনশন কত। কম রেজ্যুলেশনের ভিডিও হাই রেজ্যুলেশন মনিটরে দেখলে ছোট আকারে দেখাবে, বড় করে দেখলে ভিডিওটি ঘোলা দেখাবে।
ভিডিও’র রেজ্যুলেশনকে ভিডিও’র ফরমেটও বলা হয়। রেজ্যুলেশন অনুযায়ী ফরমেটগুলোকে এসডি, এইচডি, ফুল এইচডি, কিউএইচডি, ফোর-কে, এইট-কে ইত্যাদি নামে বোঝানো হয়। নিচে প্রচলিত বিভিন্নরকম রেজ্যুলেশন / ফরমেটের একটি চার্ট দেয়া হল ।
| Resolution Type | Common Name | Aspect Ratio | Pixel Dimension |
| SD (Standard Definition) | 480p | 4:3 | 640 x 480 |
| HD (High Definition) | 720p | 16:9 | 1280 x 720 |
| Full HD (FHD) | 1080p | 16:9 | 1920 x 1080 |
| QHD (Quad HD) | 1440p | 1:1.77 | 2560 x 1440 |
| 4K video or Ultra HD (UHD) | 4K or 2160p | 1:1.9 | 3840 x 2160 |
| 8K video or Full Ultra HD | 8K or 4320p | 16:9 | 7680 x 4320 |
ভিডিও’র রেজ্যুলেশনের ওপর ভিডিও’র গুণগত মান অনেকাংশে নির্ভর করে। কোনো ভিডিও যত বেশি রেজ্যুলেশনের তাতে বিষয়বস্তুর সূক্ষ সূক্ষ ডিটেইল তত বেশি টিকে থাকে। ভিডিও যত বেশি রেজ্যুলেশনের তা হার্ডডিস্কে তত বেশি জায়গা নেয়।
বিভিন্ন গুণাবলী’র ভিত্তিতে আরো কিছু ভিডিও ফরমেট আছে, যেমন; AVI, MPEG, MP4, AVCHD, FLV, F4V, SWE, MKV, WEBM ইত্যাদি ।
(৩) ভিডিও’র অ্যাসপেক্ট রেশিও (Aspect Ratio): এটা ভিডিও’র প্রতিটি ফ্রেমের উইডথ এবং হাইটের অনুপাতকে বুঝায়। অ্যাসপেক্ট রেশিও পিক্সেল ডাইমেনশন থেকে নির্ধারিত হয়।
স্টিল ইমেজের রেজ্যুলেশন ইচ্ছামত, যেকোনোভাবে পরিবর্তন করা যায়। ভিডিও’র রেজ্যুলেশন প্রচলিত ফরমেটের বাইরে দেয়া সম্ভব নয়। বিশেষ ফরমেটের ভিডিও বানাতে হলে ক্যামেরায় শুট করার আগেই তা ক্যামেরায় সেট করে নিতে হয়। আবার এটাও জানা প্রয়োজন, সব ক্যামেরা সব ফরমেট সাপোর্ট নাও করতে পারে। এডিটিং’র মাধ্যমে বড় ফরমেটের ভিডিওকে ছোট ফরমেটে পরিবর্তন করা সম্ভব; কিন্তু ছোট ফরমেটের ভিডিওকে বড় ফরমেটে পরিবর্তন উচিত নয়। এতে ইন্টারপোলেশন হবে, ফলে ঘোলা দেখাবে। অ্যাসপেক্ট রেশিও না মিললে ডিসটরটেড দেখাবে।
(৪)ভিডিওগ্রাফি ভার্সেস সিনেম্যাটোগ্রাফি: ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে সাধারণ কিছু ভিডিও করলেও সেটা ভিডিওগ্রাফি। পরিকল্পিত, উচ্চমানের অসাধারণ কিছু পাওয়ার জন্য সিনেম্যাটোগ্রাফি করা হয়, যার সাথে উন্নত লাইটিং, ডিরেকশন, অ্যাসথেটিক সেন্স, উন্নত এডিটিং জড়িত থাকে। সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি নির্মাণ করার সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সিনেম্যাটোগ্রাফি বলা যায়। অনেক বিয়ের ভিডিওগ্রাফি সিনেম্যাটিক স্টাইলে করা হয়ে থাকে; এগুলোও সিনেম্যাটোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে।
(৫) স্টিল ফটোগ্রাফি ভার্সেস ভিডিওগ্রাফি: স্টিল ফটোগ্রাফির সাথে ভিডিওগ্রাফির যথেষ্ট মিল আছে। ফলে যিনি স্টিল ফটোগ্রাফি শিখেছেন, তিনি খুব সহজেই এবং অল্প সময়ে ভিডিওগ্রাফি শিখতে পারেন।
স্টিল ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফির মধ্যে যেসব বিষয় একই রকম ফলাফল বহন করে, তা হল:
ক) ভিডিওর সঠিক উজ্জ্বলতা বা এক্সপোজারের জন্য অ্যাপারচার, শাটার স্পিড, আইএসও (কোনো ক্ষেত্রে DB) এবং আলোর ব্যবহার।
খ) রঙ সঠিক পাওয়ার জন্য হোয়াইট ব্যালেন্সের ব্যবহার। গ) শার্প ছবি/ভিডিও পাওয়ার জন্য ফোকাসিং, ফোকাস ট্র্যাকিং, গতিশীল অবস্থার কারণে শাটার স্পিড সিলেকশন ইত্যাদি। তবে ভিডিওগ্রাফিতে শাটার স্পিড সিলেকশনে ভিন্ন একটি নিয়ম মানা হয়, যা একটু পরে আলোচনা করা হবে। ঘ) ডেপথ অফ ফিল্ড নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় বিষয়।
ঙ) ফ্রেমে কম বা বেশি জায়গা পাওয়ার জন্য, দূরের বা কাছের বিষয়বস্তুকে ফ্রেম জুরে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ফোকাল লেংথের লেন্সের ব্যবহার।
চ) বিষয়টিকে বোধগম্য এবং দৃষ্টিনন্দন করতে কম্পোজিশনের ব্যবহার।
স্টিল ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফিতে যেসব বিষয় একটু ভিন্ন, তা হল:
ক) ভিডিও কিছুটা সময়ব্যাপী হয়ে থাকে। ভিডিও কী অবস্থায় শুরু হয়ে কী অবস্থায় শেষ হবে, তার একটা পরিকল্পনা থাকে, যাকে শট প্লানিং বলে। একটি কিংবা অনেকগুলো শট মিলিয়ে একটি ভিডিও তৈরি হতে পারে।
খ) বিভিন্ন ইফেক্ট তৈরি করার জন্য, ভিডিওকে চমকপ্রদ করার জন্য কিংবা বিষয়টিতে অধিকতর বোধগম্য করার জন্য বিভিন্নরকমের ক্যামেরা মুভমেন্ট ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণ স্টিল ফটোগ্রাফিতে নাই। একটু পরেই বিভিন্ন ক্যামেরা মুভমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
গ) ভিডিওর সাথে অডিও রেকর্ড হয়ে থাকে। সেই অডিওকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নানা রকম ব্যবস্থা নিতে হয়।
ভিডিওগ্রাফির জন্য শাটার স্পিড সিলেকশন:
ফটোগ্রাফিতে বিষয়বস্তু যত গতিশীল, মশান রার ঠেকাতে তত বেশি শাটার স্পিড সেট করতে হয়। ভিডিওগ্রাফি’র জন্য এই নিয়মটি সীমিত পর্যায়ে মানা হয়। এখানে একটি বিশেষ নিয়ম মানা হয়; তা হল, যত এফপিএস তার দ্বীগুণ শাটার স্পিড ব্যবহার করা । খুব বেশি শাটার স্পিড সেট করে ভিডিও রেকর্ড করলে ভিডিওতে এক ধরনের ঝিরিঝিরি তৈরি হয়, তাকে জিটার (Jitter) বলা হয় ।
ভিডিওগ্রাফিতে ক্যামেরা মুভমেন্ট
ক্যামেরা মুভমেন্ট বলতে পরিকল্পিতভাবে ক্যামেরাকে নড়ানো কিংবা বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা বুঝায়। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্যামেরা মুভমেন্টের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্যান (Pan): আমরা মাথা ঘুরিয়ে বাম থেকে ক্রমশ ডানে কিংবা ডান থেকে ক্রমশ বামে দেখে থাকি। রেকর্ডিং চলাকালিন ক্যামেরার অবস্থান এবং কেন্দ্র প্রায় স্থির রেখে বাম থেকে ক্রমশ ডানে কিংবা ডান থেকে ক্রমশ বামে ঘুরিয়ে নেয়াকে প্যান করা বলে। ডানে ঘোরানোকে প্যান রাইট (pan right) বামে ঘোরানোকে প্যান লেফট (pan left) বলা হয়। পাশাপাশি থাকা অনেক জিনিসকে একের পর অন্যগুলি ক্রমশ দেখাতে প্যান করা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়বস্তু ডানে কিংবা বামে যেতে থাকলে তাকে/সেটাকে ফ্রেমের যথাস্থানে রেখে ক্যামেরা প্যান করা যেতে পারে।

টিল্ট (tilt): প্যান করতে যেমন ক্যামেরার কেন্দ্র ঠিক রেখে ক্যামেরাকে ডানে/বামে ঘোরানো হয়, তেমনি টিল্টের ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে ওপর/নিচ ঘোরানো হয়। ক্রমশ ওপরে দেখানোকে টিল্ট আপ এবং ক্রমশ নিচে দেখানোকে টিল্ট ডাউন বলা হয়। একটি বহুতল ভবনের গোড়া থেকে শুরু করে ওপরিভাগ পর্যন্ত দেখাতে টিল্ট আপ এবং ওপরিভাগ থেকে শুরু করে গোড়া পর্যন্ত দেখাতে টিল্ট ডাউন করা যেতে পারে।

পেড (ped): রেকর্ডিং চলা অবস্থায় ক্যামেরাকে ক্রমশ ওপরে উঠানো কিংবা ক্রমশ নিচে নামানোকে যথাক্রমে পেড আপ এবং পেড ডাউন বলা হয়। পেড শব্দটি পেডাস্টাল (pedestal) থেকে এসেছে।

ডলি (dolly): রেকর্ডিং চলাকালে ডলি নামের ডিভাইস ব্যবহার করে ক্যামেরাকে ক্রমশ বিষয়বস্তুর দিকে এগিয়ে নেয়া কিংবা বিষয়বস্তু থেকে পিছিয়ে আসাকে ডলি বলে। এতে চাকা থাকে, স্মুথলি (ঝাঁকি না খেয়ে) সামনে কিংবা পেছনে, ডানে কিংবা বামে টানা যায়। বিষয়বস্তুর দিকে এগিয়ে গেলে সেটাকে ডলি ইন এবং বিষয়বস্তু থেকে পিছিয়ে আসলে সেটাকে ডলি আউট বলে। ডলি ইন এবং ডলি আউটকে যথাক্রমে জুম ইন এবং জুম আউটের মত দেখাতে পারে।

ট্র্যাক (track): ট্র্যাক মানে পিছু নেয়া বা অনুসরণ করা। বিষয়বস্তু যখন ক্যামেরা থেকে ডানে/বামে সরে যায়, তখন রেকর্ডিং অবস্থায় বিষয়বস্তুর সাথে দূরত্ব সম্ভবমত ঠিক রেখে ক্যামেরাকে ডানে/বামে সরানোকে ট্র্যাক করা বলে। ক্যামেরা ডানে সরানোকে ট্র্যাক রাইট এবং বামে সরানোকে ট্র্যাক লেফট বলে । ট্র্যাক রাইটকে প্যান রাইট, এবং ট্র্যাক লেফটকে প্যান লেফট’র মত মনে হতে পারে।

সার্কুলার ট্র্যাকিং (circular tracking): বিষয়বস্তুকে ফ্রেমে যথাস্থানে রেখে এর চারদিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে আনাকে সার্কুলার ট্র্যাকিং বলা হয়। ভিডিও দেখে মনে হবে, একটা বিষয়বস্তুর চারদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা হচ্ছে। এটা সম্ভব করতে সার্কুলার রেইলের সাথে ডলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জুম (zoom): জুম করতে হলে ক্যামেরায় অবশ্যই জুম লেন্স লাগানো থাকতে হবে। জুম ইন মানে হল রেকর্ডিং চলাকালে লেন্সকে ক্রমাগত টেলি’র দিকে নেয়া। জুম আউট মানে হল রেকর্ডিং চলাকালে লেন্সকে ক্রমাগত ওয়াইডের দিকে নেয়া। জুম ইন করলে মনে হয় বিষয়বস্তু ফ্রেমে ক্রমাগত বড় হচ্ছে। জুম আউট করলে মনে হয় বিষয়বস্তু ফ্রেমে ক্রমাগত ছোট হচ্ছে।
একাধিক মুভমেন্ট একত্রে ব্যবহার: বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক ক্যামেরা মুভমেন্টের মিশ্রণ ঘটানো যেতে পারে। যেমন, প্যান এবং জুম ইন। পাশাপাশি বসে থাকা কয়েকজন মানুষের বামেরজন থেকে প্যান শুরু হয়ে ডানের জেনে যাবে, একই সাথে জুম ইন করতে থাকলে ডানেরজনকে বড় করে দেখানো হবে।
ক্যামেরা মুভমেন্টে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি: খালি হাতে প্রায় সব রকমের ক্যামেরা মুভমেন্ট করা যায়, সমস্যা হয় হাত কাঁপা’র। স্মুথভাবে ক্যামেরা মুভ করার জন্য একাধিক রকমের যন্ত্র / ডিভাইস আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ট্রাইপড, ডলি, রেইল, ক্রেন/জিবস, পেডেস্টাল, ড্রোন, স্ট্যাবিলাইজার ইত্যাদি। বর্তমান যুগে কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাওয়া যায়, যা দিয়ে ক্যামেরা’র মুভমেন্ট কাছে / দূরে থেকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ফোকাস শিফটিং: ক্যামেরার সামনে ভিন্ন দূরত্বে থাকা একাধিক বিষয়বস্তুর পরপর বর্ণনা করার সময় এক একবার এক একটিতে ফোকাস করার প্রয়োজন হতে পারে, যাতে দর্শকের দৃষ্টি ফোকাস করা বিষয়টিতে পরিবর্তন হয়। ফ্রেমে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে থাকা দুইজন মানুষ যদি পালাক্রমে কথা বলে, সে সময় যখন যে কথা বলে তাকে ফোকাস করতে হয়। এভাবে ফোকাস পরিবর্তনকে ফোকাস শিফটিং বলে। টাচ ফোকাস, ফোকাস শিফটিংকে সাহায্য করতে পারে। ম্যানুয়াল ফোকাস লেন্সে চিহ্ন দিয়ে রেখে ফোকাস শিফটিং করা হয়ে থাকে।
ভিডিও’র সাথে অডিও রেকর্ডিং: ভিডিওগ্রাফি’র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভিডিও’র সাথেই অডিও রেকর্ড করা হয়ে থাকে। যেমন: সাক্ষাৎকার, অনুষ্ঠানাদি, খেলাধুলা, ওয়াইল্ড লাইফ ইত্যাদি। ভিডিওগ্রাফি’র কিছু ক্ষেত্রে অডিও আলাদা যন্ত্রে ধারণ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে অডিও অন্য সময়ে স্টুডিওতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ধারণ করা হয়। যদি ভিডিও’র সাথে ভিডিও ক্যামেরাতেই অডিও রেকর্ড করা হয়, তাহলে ভিডিওগ্রাফারকে অডিও’র মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে।
ভিডিও ক্যামেরায় কিংবা যে ক্যামেরায় ভিডিও করা যায়, তাতে বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থাকে। বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের বড় সমস্যা হল, ক্যামেরার সাথে মাইক্রোফোনটিও বক্তার কাছে থেকে আরো কাছে কিংবা দূরে চলে যায়। মাইক্রোফোন দূরে চলে গেলে বক্তার শব্দ নেয়ার জন্য অডিও লেভেল বাড়াতে হয়, অডিও লেভেল বাড়ালে আশ-পাশের অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দাদি ( ambient sound) মূল শব্দের সাথে বড় হয়ে ধরা দেয়, যা একধরনের নয়েজ হিসেবে গণ্য হয়।
ভিডিও এডিটিং: ক্যামেরায় ভিডিও নেয়ার সময় নানারকম অসঙ্গতি থেকে যায়। যেমন, একই শট একাধিকবার হয়ে যেতে পারে। শটের শুরুতে এবং শেষে অতিরিক্ত ভিডিও থাকতে পারে। এ সব কেটে-ছেটে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হয়। এক্সপোজার পরিমিত নাও হতে, বিষয়বস্তুর রঙ সঠিক নাও হতে পারে। শব্দে নয়েজ থাকতে পারে। শব্দ জোরা দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ভিডিও এডিটিং সফটঅয়ার দিয়ে এতসব ঠিক করে নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত আউটপুট বের করা যায়। একজন ভিডিওগ্রাফার নিজেই তার ভিডিও এডিট করতে পারেন; দক্ষ কোনো ভিডিও-এডিটরকে দিয়েও তা করাতে পারেন। নিজে এডিট করেন বা অন্যকে দিয়ে করান, যাই হোক, ভিডিওগ্রাফারকে এডিটিং বুঝতে হবে। এডিটিং’র মাধ্যমে কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয় তা জেনে-বুঝেই ভিডিও ধারণ করতে হবে।
ভিডিও এডিটিং’র জন্য অনেকগুলো সফটঅয়ার আছে। প্রফেশনাল এবং অ্যামেচার পর্যায়ে যে সফটঅয়ারদুটো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় তা হল: অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ( Adobe Premeire Pro) এবং অ্যাপল ফাইনাল কাট প্রো (Apple Final Cut Pro) । এ ছাড়াও ইডিয়াস এক্স প্রো, অ্যাপল আই মুভি, পিনাকল স্টুডিও, সাইবারলিংক পাওয়ার ডিরেক্টর ৩৬৫, কোরেল ভিডিও স্টুডিও আলটিমেট নামের সফটঅয়ারগুলোও ব্যবহার হয়ে থাকে।
ফটোগ্রাফার থেকে ভিডিওগ্রাফার: একজন ভালো মানের ফটোগ্রাফার খুব অল্প সময়ের মধ্যে একজন ভালো ভিডিওগ্রাফার হয়ে যেতে পারেন। ভালো হয় একজন দক্ষ ভিডিওগ্রাফারের অধীনে প্র্যাকটিস করা। তা না পেলে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারেন। তাঁকে অনেক ভিডিও দেখে বোঝার চেষ্ঠা করতে হবে। ভালো হয় কিছু বিদেশী সিনেমা দেখে ক্যামেরার কাজগুলো খুঁজে বের করা এবং অনুরূপ কোনো এফেক্ট নিজে তৈরি করার চেষ্ঠা করা। জেনে রাখবেন কাজের মান উন্নয়ন করতে হলে নিজের কাজ এক্সপার্টগণকে দেখাতে হবে এবং সমালোচনা শুনতে হবে।
Author: Rafiqul Islam
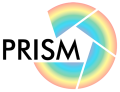



আর্টিকেলটি আমাদের জন্য অনেক সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ