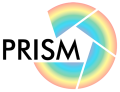একজন মানুষের জীবনে অন্য একজন মানুষ কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে বেগ স্যার এবং আমি ।
সম্ভবত ১৯৮৯ সালে বেগ স্যারের সাথে আমার প্রথম দেখা। বড় মানুষদের সাথে পরিচয় হলে একটা কথা মনে হয়, এই দেখা আরো আগে কেন হল না। দু’বছর আগে দেখা হলে এতদিনে কতই না এগিয়ে যেতাম ।

আমি তখন গ্রাফিক ডিজাইনার। তখন কম্পিউটার সিস্টেম ছিল না। হাতে এঁকে এঁকে ডিজাইন বানাতে হয়, লেখাও হাতে লিখতে হয়। মানে গ্রাফিক ডিজাইন করা এবং রঙ-তুলি দিয়ে এঁকে সাইনবোর্ড লেখার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। এই সময় ঢাকা শহরের পল্টনে বেশ কয়েকটা গ্রাফিক সিস্টেম হাউজ প্রতিষ্ঠিত হল । বারেক সাহেবের ‘কালার ডট’ এদের অন্যতম। এসব হাউজগুলোতে ম্যাকের (MAC) গ্রাফিক কম্পিউটার আনা হল । তখন কেবলমাত্র ম্যাকের কম্পিউটারে ডিজাইন ওয়ার্ক করা যেত। এখন অবশ্য উইন্ডোজেও সমস্ত কাজ করা যায়। তখন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হাতে আঁকা- জোকা করে সারাদিনে যে ডিজাইনটি প্রস্তুত করত, কম্পিউটারে ইলাস্ট্রেটর, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, কোরেল ড্র, ফটোশপ ইত্যাদি সফটঅয়ার ব্যবহার করে একজন ডিজাইনার এক ঘণ্টায় সে রকম একটি ডিজাইন উন্নত ইফেক্টসহ প্রস্তুত করতে পারত। আমরা যারা হাতে এঁকে ডিজাইন করি তাদের কপালে শনি নেমে আসল। আমার বেশিরভাগ কাস্টমার কম্পিউটারের দিকে ছুটল।
এখন কী করব? মানে কী করে খাবো । আমি তখন ফকিরাপুল এলাকায় থাকি, ফকিরাপুলেই ছিল আমাদের আব্দুর রহিম সাহেবের ‘গ্রাফিক সিসটেম’ । এখনও (২০১৭ সন) আছে। ওনাকে দেখতাম রাস্তার ধারে ক্যামেরা সেট করে জিনিসপত্রের ছবি তুলতে। বিজ্ঞাপনের কাজে জিনিসপত্রের উন্নত ছবি প্রয়োজন হতো। প্রতি বৎসর ক্যালেন্ডার ছাপার আগে ছবির জন্য সবাই রহিম ভাইয়ের কাছে ধরনা দিত । আব্দুর রহিম ভাইয়ের এই পেশা আমাকে খুব আগ্রহী করে তোলে ।
অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে সাত হাজার তিনশ টাকায় ৫০মিমি লেন্সসহ একটা Pentax K – 1000 কিনলাম। ক্যামেরা কিনলেইতো হল না; এর ব্যবহারতো জানি না । আব্দুর রহিম ভাইয়ের একজন অ্যাসিস্টেন্ট নাসির সাহেব আমাকে কিছুটা সাহায্য করতেন। মুশকিল হল তিনি নিজেই ভালো জানতেন না। আব্দুর রহিম সাহেবের কাছে যাওয়ার সাহস হত না। ভাবলাম এ সম্পর্কিত বই পড়া দরকার। অনেক খুঁজে স্টেডিয়ামের দোতলায় একটা বইয়ের দোকানে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত আধুনিক ফটোগ্রাফি নামে একটা বই পেলাম। আশ্চর্য হলাম, এই বইয়ের লেখক বাংলাদেশী, ঢাকা শহরেই থাকেন। তিনিই হলেন আমার/আমাদের মঞ্জুর আলম বেগ স্যার।
বই পড়ি আর প্র্যাকটিস করি, কিন্তু হাতে-কলমে কেউ না দেখালে বিষয়গুলো ঠিক বুঝে ওঠা যায় না । তাই শেষ পর্যন্ত বেগ সাহেবের খোঁজে বেরুলাম। অনেক লোকজনকে জিজ্ঞেস করে তাঁর ঠিকানা পেলাম; এলিফ্যান্ট রোডে এখনও (২০১৭) বেগার্ট যেখানে আছে । প্রথম দিনেই তাঁর দেখা পেলাম। পাতলা গড়নের, কালো এই গুণী মানুষটি ছিলেন গভীর ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন। প্রথম দিনের আলোচনায় আমি ছবির শার্পনেসের ওপর বাড়াবাড়ি কিছু বলছিলাম । তিনি বোঝালেন, ছবির শার্পনেস যেমন গুরুত্বপুর্ণ, ছবির কিছু জায়গা ঘোলা হওয়া বা ঘোলা করতে পারাও তেমনি গুরুত্বপুর্ণ।
বেশ কয়েকদিন সাক্ষাতের পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, স্যারের কাছে ফটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করার। তিনি রাজি হলেন, যদিও আমার বেসিক কোর্স করা ছিল না। আমার সাথে আরেকজন ছাত্র ডিপ্লোমার ক্লাস করতেন।
বেগ স্যার ছিলেন আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের একজন। অনেক জটিল বিষয় পানির মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন তিনি। কোনো বিষয় কীভাবে শেখাবেন, তা নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। কোনো কিছু শেখানোর পর তিনি প্রচুর হোম ওয়ার্ক দিতেন । ফটোগ্রাফির গুরুত্বপুর্ণ বিষয় আমাকে কীভাবে শিখিয়েছিলেন, সেই সব অভিজ্ঞতার কথা আজো মনে পড়ে ।
এনলার্জার দিয়ে এক্সপোজার শেখালেন: এক্সপোজার বিষয়টি শেখাতে তিনি আমাকে সরাসরি ডার্করুমে ঢোকালেন । এনলার্জার দিয়ে নেগেটিভ থেকে ফটোপেপারে প্রিন্ট করে ক্যামেরায় অ্যাপারচার, শাটার স্পিড এবং আইএসও’র ধারণা দিলেন। তিনি অ্যাপারচার ছোট-বড় করে দেখালেন, কীভাবে প্রজেকশনটি কম এবং বেশি আলোকিত দেখায়। ফটোর পেপারের ওপর প্রজেকশনটি বেশিক্ষণ রাখলে প্রিন্ট বেশি গাঢ় হয়, কম সময় রাখলে প্রিন্ট হালকা হয়। বিষয়টিকে ক্যামেরার শাটার স্পিডের সাথে তুলনা করে বোঝালেন। কোনো ক্যামেরায় শাটার স্পিড কিংবা অ্যাপারচারের ইফেক্ট সরাসরি দেখা যায় না। অতএব এনলার্জার দিয়ে দেখানোর বিষয়টি খুবই যৌক্তিক ছিল ।
তিনি ফিল্মের গ্রেইন বোঝালেন: যাঁরা ফিল্মে কাজ করেছেন, তাঁরা সবাই জানেন বেশি আইএসও নাম্বারের ফিল্মে বেশি গ্রেইন হয় (এখন ডিজিটালে বেশি আইএসও ব্যবহার করলে ছবি নয়েজি হয়)। ফাইন গ্রেইন এবং কোর্স গ্রেইন বিষয়টি বোঝাতে তিনি মজার একটি কাজ করলেন। মসুরের ডাল ঢেলে দিয়ে একটি নকশা আঁকালেন। অড়হর ডাল দিয়ে পাশেই একই নকশা আঁকালেন । এবার পাঁচ ফুট দুর থেকে নকশা দুটোকে দেখতে বললেন । পাঁচ ফিট দূর থেকে মসুরের দানাগুলো আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছিল না, ফ্ল্যাট বা স্মুথ মনে হচ্ছিল। কিন্তু অড়হর দানাগুলো বড় হওয়াতে পাঁচ ফিট
দূর থেকেও সেগুলো আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছিল। বেগ সাহেব মসুরের ডাল দিয়ে আঁকানো নকশাটিকে ফাইন গ্রেইন এবং অড়হর ডালে আঁকা নকশাটাকে কোর্স (মোটা) গ্রেইন হিসেবে তুলনা করে বোঝালেন।
এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড পরীক্ষা: ফিল্মের এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড বলে একটা ব্যাপার ছিল। ডিজিটালেও ল্যাটিচ্যুড বিষয়টি আছে। ফিল্মের এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড বোঝাতে গিয়ে তিনি আমাকে তাঁর নিজের স্টক থেকে ১২ আইএসও’র একটি সাদাকালো (রাশিয়ায় তৈরী) ফিল্ম দিলেন। আমাকে ১০০ আইএসও’র একটি সাদাকালোফিল্ম কিনতে বললেন। এরপর আমার ব্যবহারিক কাজটা এ রকম ছিল: ক্যামেরা থেকে ৫ ফিট, ১০ ফিট, ১৫ ফিট এবং ২০ ফিট দুরে পরপর একই/একই রকম উজ্জ্বল চারটি জিনিস থাকবে। আলো একেবারে কম এ রকম জায়গায় ক্যামেরা স্ট্যান্ডে রেখে সরাসরি ফ্ল্যাশে ১০০ আইএসও ফিল্মে ১০ ফিট দূরের জিনিসটি অনুযায়ী এক্সপোজার ঠিক করে একবার ছবি তোলা হবে । এবার ১২ আইএসও ফিল্ম ক্যামেরায় তুলে সে অনুযায়ী এক্সপোজার যথাযথ পরিবর্তন করে আরেকটি ছবি তোলা হবে । ছবি যথা নিয়মে তুলে ফিল্মটা প্রসেস করলাম। ১০০ আইএসও এবং ১২ আইএসও নেগেটিভ থেকে আলাদা দুটি প্রিন্ট করলাম। প্রিন্ট দুটি পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। ১০০ আইএসও নেগেটিভ থেকে পাওয়া প্রিন্টে পাঁচ ফিট থেকে শুরু করে বিশ ফিট দূরের জিনিসটি পর্যন্ত স্পষ্ট ছিল; অর্থাৎ পাঁচ ফিট দূরের জিনিসটি ওভার এক্সপোজ হয়ে একবারে সাদা হয়ে যায়নি, আবার বিশ ফিট দূরের জিনিসটি পুরোপুরি কালো হয়ে যায়নি, উভয়টিকে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছিল। অন্য দিকে ১২ আইএসও নেগেটিভ থেকে করা প্রিন্টটিতে পাঁচ ফিট দূরের জিনিসটি ওভার এক্সপোজ হয়ে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর বিশ ফিট দূরের জিনিসটি পুরোপুরি কালো হয়ে গিয়েছিল । শুধুমাত্র দশ ফিট দূরের জিনিসটিতে ভালো ডিটেইল ছিল আর পনের ফিট দূরের জিনিসটি প্রায় কালো হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার বাসায় ডার্করুম, সাদাকালো প্রিন্ট করার জন্য এনলার্জার, পেপার, প্রসেস কেমিকাল সবই ছিল। ফলে স্যারের দেয়া অ্যাসাইনমেন্টগুলো বাসায় সেরে ফেলতে পারতাম।

পরদিন নেগেটিভ এবং প্রিন্ট নিয়ে স্যারের কাছে গেলাম । তিনি বোঝালেন; ১০০ আইএসওতে অনেক ওভার এবং অনেক আন্ডার এক্সপোজারেও (প্রায় চার স্টপের/ষোল গুণ পার্থক্যে) ডিটেইল ধরে রেখেছে । মানে ১০০ আইএসও ফিল্মের (বেশি আইএসও) এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড বেশি । অন্যদিকে ১২ আইএসও ফিল্ম অনেক ওভার এবং অনেক আন্ডার এক্সপোজারে ডিটেইল ধরে রাখতে পারে নাই । মানে ১২ আইএসও ফিল্মের (কম আইএসও) এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড অনেক কম। তিনি এটাও বোঝালেন, ফিল্মের কন্ট্রাস্ট যত বেশি এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড তত কম । অপূর্ব! আমার কাছে এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড বিষয়টি পরিশ্রুত পানির মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। এক্সপোজার ল্যাটিচ্যুড নিয়ে নতুন করে কিছু শিখতে হয়নি।
লেন্সের ফোকাল লেংথ অনুযায়ী তৈরী হওয়া পার্সপেকটিভ পরীক্ষা: লেন্সের ফোকাল লেংথ এবং সাবজেক্টের দূরত্ব অনুযায়ী ছবিতে পার্সপেকটিভ পরিবর্তন হয়ে থাকে। আমার পেনটাক্স কে-১০০০ এর সাথে ২৮মিমি (ওয়াইড), ৫০ মিমি (নরমাল) এবং ৭০-২০০ মিমি (টেলি টু টেলি জুম) লেন্স টেলি ছিল। স্যারের নির্দেশ অনুযায়ী আমি একটি মুখমণ্ডলের চিন থেকে ক্রাউন (টাইট ফ্রেমে) ২৮, ৫০ এবং ২০০ মিলিমিটার ফোকাল লেংথে ছবি তুললাম। ২৮ মিলিমিটার ফোকাল লেংথে ছবি তুলতে মুখমণ্ডলের একদম কাছে যেতে হল । ৫০ মিলিমিটার ফোকাল লেংথে ছবি তুলতে একটু দূরে এবং ২০০ মিলিমিটার ফোকাল লেংথে ছবি তুলতে বেশ দূরে (প্রায় পাঁচ ফিট) যেতে হল । মডেল হিসেবে আমার মেজো ছেলেকে ব্যবহার করলাম। মজার ব্যাপার আমি যখন আমার লেখা বই প্রস্তুত করি, তখন ঐ ছবিগুলোই ব্যবহার করেছি।
ফোকাল লেংথের ব্যবহারের ওপর তিনি আরেকটি পরীক্ষা দিলেন । বললেন, ক্যামেরা নিয়ে আপনাকে (তিনি ছোট বড় সবাইকে আপনি সম্বোধন করতেন) সংসদ ভবন যেতে হবে । ওখান থেকে কম বয়সের একটি ছেলে যোগাড় করবেন। ছেলেটিকে একই জায়গায় দাড় করে রেখে দুটি ছবি তুলবেন। একটি ছবিতে ছেলেটি অনেক বড়, সে তুলনায় সংসদ ভবন ছোট দেখা যাবে। অন্য ছবিটিতে ছেলেটি ছোট এবং সংসদ ভবনকে বড় হতে হবে। প্ৰথম ছবিটি তুলতে আমাকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহার করতে হল, ছেলেটিকে ক্যামেরার কাছে রাখতে হল । দ্বিতীয় ছবিটি তুলতে নরমাল লেন্স ব্যবহার করতে হল, ছেলেটিকে ক্যামেরা থেকে দূরে রাখতে হল। লেন্সের ফোকাল লেংথ কীভাবে ছবির কম্পোজিশন পরিবর্তন করে ফেলে সে ব্যাপারে এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। জীবনে কখনও ভুলিনি, হয়ত ভুলব না।
আমার জীবনে হাতে গোনা দু-চার জন শিক্ষককে পেয়েছিলাম, যাদের শেখানোর পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত লাগসই । আমাদের বেগ স্যার ছিলেন তাদের মধ্যেও সেরা। আমার শিক্ষকতা জীবনে তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে তাঁর মতো শিক্ষকের বার বার জন্ম হোক, সেটাই প্রত্যাশা।
Author: Rafiqul Islam, FBPS Writer.