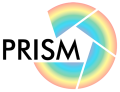টেকনোলজির উন্নয়নের সাথে ফটোগ্রাফির জগতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানান প্রশ্ন এবং বিতর্কের ঝড় ওঠে। এই বছর কয়েক আগেও একটা বিতর্ক দেখে আসলাম, তা ছিল ফিল্ম ভার্সেস ডিজিটাল। সেই বিতর্ক শেষ হতে না হতেই কয়েক বছর হল এখন আরেকটা বিতর্ক দানা বেঁধে উঠেছে; তা হল ডিএসএলআর ভার্সেস মিররলেস।
মিররলেস ক্যামেরা প্রথম বাজারজাত হয় ২০০৪ সালে (Epson R-D1)। তবে আমাদের দেশে বহুল ব্যবহার ও আলোচনা শুরু হয় ২০১৬ সাল থেকে। শুরুতে এমনটা মনে করা হত না, মিররলেস এক সময় ডিএসএলআরের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। ১৯৮০’র দশকের শেষে যাত্রা শুরু করা ডিএসএলআর ক্যামেরা ২০১৭ তে মিররলেস জনপ্রিয় হওয়া এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক শক্ত অবস্থানেই ছিল । ২০২২-এ মিররলেস তার সক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে ফটোগ্রাফির বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।
ফিল্ম ফটোগ্রাফির বিদায়ের পর ডিজিটাল ক্যামেরার দুটি ধরন ছিল, একটি কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরা, অপরটি এসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরা। এসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরাকে সংক্ষেপে ডিএসএলআর ক্যামেরা বলা হয় ।
কম্প্যাক্ট ক্যামেরা বহুল প্রচলিত। এখনও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৌখিন ব্যবহারকারী কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করেন । মোবাইল ফোনের সাথে সংযুক্ত ক্যামেরাগুলো ও কম্প্যাক্ট ক্যামেরার অনুকরণে তৈরি T
কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরার বৈশিষ্ট্যগুলো হল:
১) ক্যামেরার সাথে লেন্সটি ফিক্সড করা, পরিবর্তনযোগ্য নয়। লেন্সটি সাধারণত একটি ওয়াইড টু টেলি জুম লেন্স হয়ে থাকে, যা ছবি তোলার সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে পারে।

২) ছবি তোলার আগে ছবির বিষয়টি দেখা যায় এলসিডি মনিটরে কিংবা ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডারে। এলসিডি মনিটরে যা দেখা যায়, ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডারে তারই একটি ছোট ভার্সন দেখা যায়। কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরায় এসএলআর ক্যামেরার মত কোনো মিররের ব্যবহার নাই, লেন্স হয়ে দৃশ্যের প্রজেকশন সরাসরি ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরে গিয়ে পড়ে। ইমেজ সেন্সর থেকে দৃশ্যের ভিডিও চিত্র ক্যামেরার এলসিডি মনিটরে কিংবা ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডারে দেখানো হয়। এই ভিডিওটি রেকর্ড/সেইভ হয় না, শুধু তাৎক্ষণিক দেখার জন্য। এ জন্য এটাকে আনরেকর্ডেড ভিডিও বলা হয়।
৩) কম্প্যাক্ট ক্যামেরাগুলোর বেশিরভাগই সাইজে ছোট, ওজনও কম, এর ইমেজ সেন্সরও বেশ ছোট। সেন্সর বেশ ছোট হওয়াতে অল্প জায়গাতে ফটোডায়ডগুলোকে সাজানো থাকে। মানে, ফটোডায়ডের ঘনত্ব খুব বেশি। ফলে আইএসও অল্প বাড়ালেই ছবিতে নয়েজ খুব বেড়ে যায়। তবে কম্প্যাক্ট ক্যামেরার কিছু কিছু মডেল এসেছে যেগুলোর সেন্সর সাইজ ডিএসএলআরের মত বড় ।
ডিজিটাল এসএলআর (ডিএসএলআর) ক্যামেরার বৈশিষ্ট্যগুলো হল:
১) যে কোনো সময় লেন্স পরিবর্তন করা যায়, লেন্স এবং ক্যামেরা বড়ি আলাদা করেও রাখা যায়। এই সুবিধাকে লেন্স ইন্টারচেঞ্জেবিলিটি বলা হয় ।
২) লেন্সের মাধ্যমে দৃশ্যের প্রজেকশন প্রথমে ৪৫ ডিগ্রিতে সেট করা একটি মিররে গিয়ে পড়ে, সেই প্রজেকশনটি ঐ মিরর থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে ক্যামেরার ওপরিভাগে থাকা পেন্টাপ্রিজম বা পেন্টামিররে ঢোকে। পেন্টাপ্রিজম বা পেন্টামিররের ভিতর দৃশ্যটি দুবার রিফ্লেক্ট হয়ে ভিউ ফাইন্ডারে আসে। দৃশ্য দেখানোর এই ব্যবস্থা পুরোটাই অপটিক্যাল, মানে অপটিক্স’র সাহায্যে; কোনো ইলেকট্রনিক সহযোগিতা ছাড়াই। সোজা কথায় বলা হয়, ডিএসএলআর ক্যামেরার ভিউয়িং সিসটেম অপটিক্যাল। এর ভিউ ফাইন্ডারকে অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডার বলা হয়। ক্যামেরা অফ থাকা সময়ও ভিউ ফাইন্ডারে দৃশ্য দেখা সম্ভব হয় ।
৩) ডিএসএলআর ক্যামেরা কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরার তুলনায় বেশ বড়। মিরর এবং পেন্টাপ্রিজম এই দুটি অপটিক্যাল ব্যবস্থাকে জায়গা দিতে ক্যামেরার আয়তন বেড়ে যায়, সাথে সাথে ওজনও। ডিএসএলআর ক্যামেরায় সাধারণত দু’রকম সাইজের ইমেজ সেন্সর ব্যবহৃত হয়। একটি হল ডিএক্স (নাইকনে)। ডিএক্স’র প্রায় সমান সাইজের সেন্সরকে ক্যাননে বলা হয় এপিএসসি। আরেকটি সাইজ হল, এফএক্স (নাইকনে)। এফএক্স’র সমান সাইজের সেন্সরকে ক্যাননে বলা হয় এফএফ।
ডিএসএলআর ক্যামেরায় সেন্সর বড় হওয়াতে এর ইমেজ কোয়ালিটি কম্প্যাক্টের তুলনায় অনেক ভালো হয়ে থাকে। অনেক বেশি আইএসওতেও ছবিতে খুব একটা নয়েজ হয় না । ইমেজ সেন্সর বড় হওয়ায় সিলেটিভ ফোকাস ইফেক্ট তৈরি করা যায় সহজেই।
আলোচনা করার কথা ডিএসএলআর এবং মিররলেস ক্যামেরা নিয়ে, সেখানে কম্প্যাক্ট ক্যামেরাকে টানলাম কেন? হ্যা, প্রয়োজন আছে। আমি বলতে চাই কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ডিএসএলআর ক্যামেরার সমস্যার বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে এবং সুবিধাজনক ফিচারগুলোকে সন্নিবদ্ধ করেই মিররলেস ক্যামেরার উৎপত্তি ঘটানো হয়েছে।
কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরায় যে সব সমস্যা আছে
১) লেন্স পরিবর্তন করা যায় না, নির্দিষ্ট ফোকাল লেংথের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।
২) সকল মডেলে সব ধরনের অ্যাক্সেসরিজ (ফিল্টার, এক্সটারনাল ফ্ল্যাশ, রিমোট ইত্যাদি) ব্যবহার করা যায় না।
৩) সেন্সর ছোট হওয়াতে আইএসও ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আছে। আইএসও অল্প বাড়ালেই ছবিতে নয়েছে হয়।
৪) সেন্সর ছোট হওয়াতে ডেপথ অফ ফিল্ড খুব একটা কমানো যায় না। মানে, সিলেকটিভ ফোকাস ইফেক্ট তৈরি করা প্রায় অসম্ভব।
৫) বেশিরভাগ কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরাতে ম্যানুয়াল ফোকাস করা সম্ভব হয় না।
৬) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাটার ল্যাগ হয়ে থাকে। মানে, শাটার চাপার পর ছবি উঠতে অল্প একটু (সেকেন্ডের ফ্রাকশন) সময় নেয়। গতিশীল বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো মুহূর্তের ছবি তোলায় সঠিক মুহূর্তটি বাদ পড়ে যায়।
৭) কন্টিন্যুয়াস মোডে এফপিএস (ফ্রেমস পার সেকেন্ড) তুলনামূলকভাবে কম ।
৮) ফোকাসিং খুব একটা ফাস্ট নয়।
৯) কোনো কোনো মডেলে এক্সটারনাল ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা গেলেও, অফ ক্যামেরা ফ্ল্যাশ (ক্যামেরা থেকে আলাদাভাবে জ্বলা ফ্ল্যাশ) ব্যবহার করা যায় না অথবা জটিলতাপূর্ণ। ফলে স্টুডিও স্ট্রোবে ছবি ভোলা প্রায় অসম্ভব।
কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরায় যে সব সুবিধা আছে:
১) ছবি তোলার পর এক্সপোজার, হোয়াইট ব্যালেন্সসহ অন্যান্য ইমেজ সেটিংস-এর যে ফলাফল পাওয়া যাবে, ছবি ভোলার আগেই ক্যামেরার এলসিডি মনিটরে একই অবস্থায় দৃশ্য দেখা (প্রিভিউ) যাবে। অ্যাপারচার ছোট দেয়ার কারণে যদি এক্সপোজার আন্ডার হতে যায়, ছবি তোলার আগেই মনিটরে দেখা দৃশ্যে সরাসরি তা বোঝা সম্ভব। এ রকম হোয়াইট ব্যালেন্স ভুল সেটিং-এর জন্য যদি কালার কাস্ট হতে যায়, ছবি তোলার আগেই সরাসরি তা দেখা যায় ।
২) ক্যামেরা আয়তনে এবং ওজনে কম হওয়ায় বহন করা সুধিজনক। কোনো কোনো মডেলের কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরা পকেটে রাখাও সম্ভব।
৩) কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরার শাটার ব্যবস্থা ইলেকট্রনিক। অ্যাপারচার সব সময় সেট করা সাইজেই থাকে। ফলে শাটার পড়ার শব্দ নাই বললেই চলে। কোনো ক্ষেত্রে রেকর্ড করা শব্দ বাজে। ছবি তোলার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাটারের শব্দ কম হলে বা না হলে সুবিধা হয়।
৪) কম্প্যাক্ট ক্যামেরা আনাড়ী ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
ডিএসএলআর ক্যামেরায় যে সব সমস্যা আছে
১) ডিএসএলআর ক্যামেরার লেন্সে অটো-অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম ব্যবস্থা কাজ করে। মানে অ্যাপারচার ছোট বা বড় যাই সেট করা হোক, লেন্সের সবচেয়ে বড় অ্যাপারচার সেট করলে ছবি যেমন হওয়ার কথা, অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডারে সে রকম অবস্থায় দৃশ্যকে দেখায়। সেট করা অ্যাপারচারে ডেপথ অফ ফিল্ড কী দাড়াচ্ছে, তা বোঝা সম্ভব নয়।”
২) লেন্সে অটো-অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম ব্যবস্থা কাজ করার কারণে ছবি আন্ডার অথবা ওভার হতে যাচ্ছে কি না, অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডারে দৃশ্য দেখে তা সরাসরি বোঝার উপায় নাই। দৃশ্যটা কম এক্সপোজারে কিংবা বেশি এক্সপোজারে একই রকম দেখায়। এক্সপোজার সঠিক, আন্ডার বা ওভার হওয়ার সংকেত পেতে হয়, এক্সপোজার ফেল দেখে ।
৩) অপটিক্যাল ভিউয়িং কার্যকর করতে ক্যামেরা বডিতে বেশ বড় আকারের একটি মিরর সেট করা থাকে। ছবি ওঠার মুহূর্তে এটি ওপরে উঠে চেপে থাকে। শাটার রিলিজ হয়ে গেলে সেটি নেমে আসে। এই মিররটি লেন্স দিয়ে প্রজেকশন হওয়া
দৃশ্যটাকে প্রতিফলিত করে নব্বই ডিগ্রি ওপরের দিকে পেন্টা- প্রিজম, ক্যামেরাভেদে পেন্টামিররে পাঠায়। মিররে প্রতিফলন হওয়ার সময় দৃশ্যটি হরাইজন্টালি এবং ভার্টিকালি ফ্লিপড হয়ে যায়। পেন্টা-প্রিজম বা পেন্টা-মিরর ফ্লিপ হওয়া দৃশ্যকে আনফ্লিপ করে নিয়ে ভিউ ফাইন্ডারে পাঠায়, যেখানে চোখ লাগিয়ে আনফ্লিপ দৃশ্যটা দেখি ।
কিন্তু এতে সমস্যা কী? সমস্যাটা হল, মিরর ধারণ করা, মিররের উঠানামা, পেন্টা-প্রিজম কিংবা পেন্টামিরর এত সবের জন্য ক্যামেরার ভেতরে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। ওজনও হয়ে যায় প্রায় দিগুণ ।
মিররলেস ক্যামেরা তা হলে কেমন?
গঠনগত দিক থেকে কম্প্যাক্ট ক্যামেরাগুলোও এক ধরনের মিররলেস ক্যামেরা, যেহেতু এর ভেতরে মিররের ব্যবহার নাই । তবে সময়ের প্রেক্ষিতে মিররলেস ক্যামেরা বললে বুঝতে মিররলেস ইন্টারচেঞ্জেবল লেন্স ক্যামেরা; সংক্ষেপে হবে, এমআইএলসি (MILC)।
যদি বলা হয়, একটা কম্প্যাক্ট ক্যামেরায় ফিক্সড লেন্সটি খুলে ফেলে সেখানে এসএলআর ক্যামেরার মত লেন্স মাউন্ট ব্যাবস্থা সংযোজন করা হল, ছোট আকারের সেন্সরের জায়গায় বড় আকারের সেন্সর যুক্ত করা হল। তা হলে এটা মিররলেস ক্যামেরাই হয়ে দাড়ালো ।
আবার যদি বলা হয়, একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা থেকে অপটিক্যাল ভিউয়িং সিস্টেম বাদ দেয়া হল। ক্যামেরাটার আয়তন এবং ওজন প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডারের জায়গায় ছোট আকারের হাই রেজ্যুলেশন মনিটর সেট করা হল। এলসিডি মনিটরে লাইভ ভিউয়িং-এর সময় যে ভাবে দৃশ্য দেখানো হয়, সেই দৃশ্যই ভিউ ফাইন্ডারে দেখানোর ব্যবস্থা করা হল । ভিউ ফাইন্ডারটির নতুন নামকরণ করা হল, ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার। তা হলে এটা মিররলেস ক্যামেরাই হয়ে গেল ।
মিররলেস ক্যামেরার যা যা বৈশিষ্ট্য দাড়ালো
১) ডিএসএলআর ক্যামেরা বডির তুলনায় মিররলেস ক্যামেরা বডির ওজন এবং আয়তন প্রায় অর্ধেক।
২) ছবি তোলার পর ছবিটি যেমন হবে, ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডারে কিংবা এলসিডি মনিটরে অবিকল সেই ছবিই দেখা যায়। মানে, ছবি আন্ডার বা ওভার এক্সপোজ হতে গেলে কিংবা
কালার কাস্ট হতে গেলে ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডারে কিংবা এলসিডি মনিটরে দেখে তা সরাসরি বোঝা যায় ।
৩) মিররের ওঠা-নামা না থাকায় এবং ইলেকট্রনিক শাটার ব্যবহার হওয়ায় শাটার রিলিজের শব্দ খুবই কমে যায় ।
৪) ডিএসএলআর ক্যামেরার মত যখন তখন লেন্স পরিবর্তন করা যায়।
৫) কোনো মিররলেস ক্যামেরার ইমেজ সেন্সর যদি কোনো ডিএসএলআর ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরের সমান হয়, তবে তাদের ইমেজ কোয়ালিটিতে পার্থক্য হওয়ার কোনো যুক্তি নাই । ৬) ভিডিও করার জন্য এখানে লাইভ ভিউয়ে শিফট করার প্রয়োজন নাই, কারণ এটা অন করলেই লাইভ।
৭) মিররলেস ক্যামেরায় ভিডিও’র জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা আছে, যা ডিএসএলআরে নাই। মিররলেস ক্যামেরার কিছু মডেলে 4K ভিডিও করার সুযোগ আছে।
মিররলেস ক্যামেরার এই বেশিষ্ট্যগুলো ফটোগ্রাফারদের জন্য সুবিধাই বটে। তবে সব ভালো’র দু-চারটে মন্দ দিক থাকে।
মিররলেস ক্যামেরার কিছু সমস্যা
১) ডিএসএলআর ক্যামেরার জন্য যত রকমের লেন্স পাওয়া যায়, মিররলেস ক্যামেরার জন্য অত রকমের লেন্স এখনও তৈরী হয় নাই। তবে সুবিধার কথা হল, একটা অ্যাডাপ্টর ব্যবহার করে ডিএসএলআর ক্যামেরার যে কোনো লেন্স একই ব্র্যান্ডের মিররলেস ক্যামেরায় ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া মিররলেস ক্যামেরার জন্য তৈরী লেন্সের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে।
২) কম্প্যাক্ট ডিজিটাল ক্যামেরার মত মিররলেস ক্যামেরাতেও কিছু না কিছু শাটার ল্যাগ হয় । তবে এটা এতটাই কমিয়ে আনা হয়েছে যে, ঐটুকুতে সমস্যা হয় না।
৪) মিররলেস ক্যামেরার বডি ছোট, ব্যাটারি চ্যাম্বার ছোট, ব্যাটারিও ছোট। ডিএসএলআরের ব্যাটারি সে তুলনায় অনেক বড়। অথচ অপটিক্যাল ভিউ ফাইন্ডার ব্যবহারের কারণে বিদ্যুৎ খরচ খুব কম । মিররলেস ক্যামেরায় ইলেকট্রনিক ভিউ ফাইন্ডার ব্যবহার হওয়ায় অনেক বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়। এ জন্য পুরো চার্জ দেয়া একটি ব্যাটারি দিয়ে বেশিক্ষণ ছবি তোলা যায় না। এ জন্য ক্যামেরা ব্যবহারকারীকে অতিরিক্ত ব্যাটারি কিনতে হয় এবং সাথে রাখতে হয়।
প্রস্তুতকারকরা কোন দিকে এগুচ্ছে?
যতদূর বোঝা যায় ক্যামেরা প্রস্তুতকারকরা তাদের মিররলেস ক্যামেরাগুলোর উন্নতিসাধনে ব্যস্ত। বলা যায় না, এক সময় ডিএসএলআরের নতুন মডেল তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
আমরা ডিএসএলআর ব্যবহারকারীরা কী করব?
আমরা ডিএসএলআর ব্যবহারকারীরা ক্যামেরা, লেন্স এবং অ্যাক্সেসরিজের পেছনে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শিফ্ট করার মধ্যে নাই। কারণ ডিএসএলআর দিয়ে কাজ চলছে, ভালোভাবেই চলছে। আমাদের যা আছে, তা দিয়ে ছবি তুলে যাই। মেটাডাটা না খোলা পর্যন্ত বোঝার উপায় নাই, ছবি কোন ক্যামেরায় তোলা। তবে যারা নতুন শুরু করবে, তাদের কথা ভিন্ন, তারা মিররলেসের পেছনে ঝুঁকবে, সেটাই স্বাভাবিক।
ডিএসএলআর কিংবা মিররলেস যা-ই হোক, ক্যামেরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত, তা হল :
১) ইমেজ কোয়ালিটি: ক) কত মেগাপিক্সেল, খ) যথাযথ রঙ রিপ্রোডাকশনের ক্ষমতা, গ) নয়েজবিহীন ছবি প্রদানের ক্ষমতা, ঘ) ডাইন্যামিক রেঞ্জ ।
২) গুরুত্বপুর্ণ অ্যাক্সেসরিজসমূহ ব্যবহার করা যায় কি না। যেমন: ফ্ল্যাশ, ফিল্টার, রিমোট, ট্রাইপড ইত্যাদি।
৩) ব্যবহার পদ্ধতি কতটা সহজবোধগম্য ।
৪) ইতপূর্বে ব্যবহৃত ক্যামেরার সাথে কতটা মিল।
৫) সর্বোচ্চ এফপিএস কত।
৬) শাটার স্পিড রেঞ্জ ।
৭) ফোকাসিং কতটা ফাস্ট এবং ফোকাসিং’র আধুনিক সুবিধাগুলো আছে কি না ।
৮) হাতে নিয়ে ছবি তোলা কতটা আরামদায়ক।
৯) দেখতে কতটা সুন্দর ।
১০) ভিডিও কোয়ালিটি ।
১১) ব্যবহারের ক্ষেত্রের সাথে কতটা সংগতিপুর্ণ।
১২) মূল্য ।